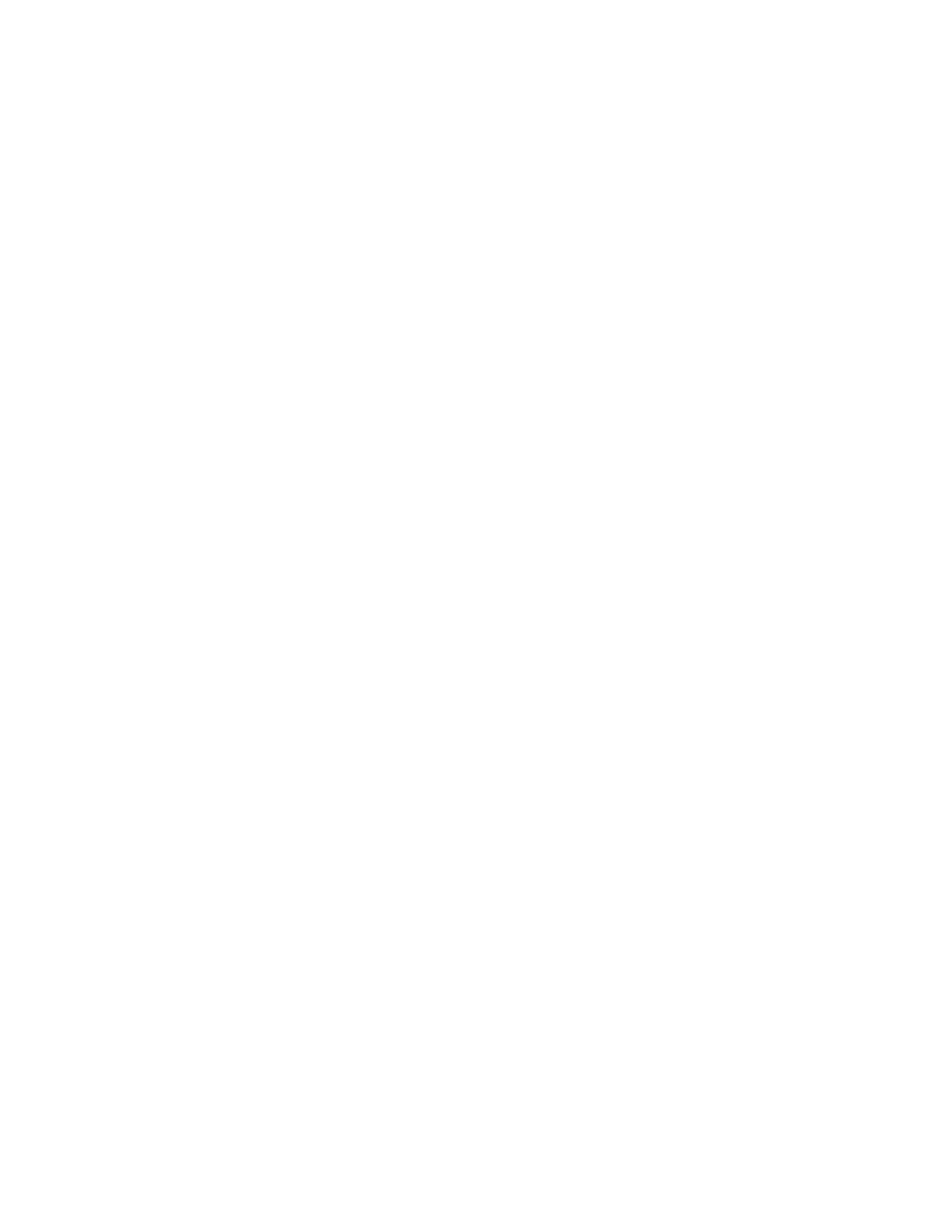রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ভাবনা
পঞ্চানন মন্ডল
May 20, 2025 | | views :4 | like:0 | share: 0 | comments :0
রবীন্দ্রনাথের কাছে বিজ্ঞান ছিল সংস্কৃতিরই একটা অঙ্গ। বিজ্ঞানের মাঝে লুকিয়ে থাকা সাহিত্য সংস্কৃতিকে বারংবার চিনে নিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর জীবন দর্শনে বার বার প্রতিফলিত হয়েছে বিজ্ঞানমনস্কতা।
মাত্র সাড়ে বারো বছর বয়সে ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি অস্বাক্ষরিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ লেখেন- ‘গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি’। অনেকে বলেন যে, গ্রহগণ জীবের আবাসভূমিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ অন্তত দু’ জায়গায় সেই কিশোর বয়সে লেখা রচনাটির উল্লেখ করেছিলেন। এই লেখার অনেক অনেক বছর পর শেষ বয়সে এসে কবিগুরু একশ’ পনেরো পৃষ্ঠার আরেকটি বিজ্ঞানভিত্তিক বই প্রকাশ করেন, ‘বিশ্বপরিচয়’। শুধু তা-ই নয়, তিনি বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার কৃতি শিক্ষক ও ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে।
রবীন্দ্রনাথ তার উৎসর্গপত্রে লিখলেন—
‘বয়স তখন হয়তো বারো হবে, পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ডালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলোয়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে গিরিগৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছিলুম। স্বাদ পেয়েছিলুম বলে লিখেছিলুম। জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।’
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। একজন মহাকবির সাথে এক মহাবিজ্ঞানীর দেখা হতেই হবে। যদিও বয়সের একটা বড় ব্যবধান ছিল। সেটা ১৯৩০ সাল। রবীন্দ্রনাথ ঊনসত্তর বছর পেরিয়ে সত্তরে পা দিয়েছেন। আইনস্টাইনের বয়স তখন বাহান্ন। রবীন্দ্রনাথের থেকে আইনস্টাইন ১৮ বছরের ছোট ছিলেন। ১৯৩০ সালেই রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতা দিতে গিয়ে ‘সভ্যতার সংকট’ পাঠ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে কবি ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া ও পারস্যে তাঁর চিত্রকর্ম নিয়ে যান। বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হবার আগে রবীন্দ্রনাথ কি আইনস্টাইনকে জানতেন? জানতেন বৈকি।
১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল সংঘটিত হয় ইতিহাসের জঘন্যতম জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। এই বর্বরতার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ‘নাইট’ উপাধি পরিত্যাগ করলেন।
১৩ এপ্রিল অমৃতসরের চারদিকে পাকা প্রাচীরের ভেতর চলছিল একটি ব্রিটিশবিরোধী সভা। বের হবার পথ ছিল একটাই। হঠাৎ ব্রিটিশ সামরিক অফিসার জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য বেপয়োরা গুলি বর্ষণ করে। ১৬০০ রাউন্ড গুলি চালানোর পর গুলি ফুরিয়ে যায়। এই হত্যাকাণ্ড এমনি জঘন্য ছিল কতজন মারা গিয়েছিল তার চেয়ে দেখার ছিল কতজন বেঁচে ছিল। যাইহোক, গভর্নর জেনারেলের একজন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য স্যার শঙ্করণ নায়ার বার্ষিক চৌষট্টি হাজার টাকার বেতনের চাকরিতে ইস্তফা দেন; কিন্তু ‘নাইট’ খেতাব বর্জন করেননি। অথচ পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে চাকরি ত্যাগ করার জন্য স্যার শঙ্করণ নায়ারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করা হলেও ‘নাইট’ ত্যাগ করার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করতে দেওয়া হয়নি। ১৯১৯ সালেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে নোবেলজয়ী সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ যখন মানুষের স্বাধীনতা বিষয়ক দলিল তৈরি করেছেন, সেই দলিলে স্বাক্ষরকারী মানুষদের মধ্যে দু’জন মানুষের নাম ছিল রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন।
১৯০২, সালের ১০ মে বিশ্বনন্দিত বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু রয়্যাল ইনস্টিটিউটে ‘যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড়পদার্থের সাড়া’ বিষয়ক গবেষণাপত্র পাঠ করেছিলেন। তার দশদিন আগে ১ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লন্ডন থেকে জগদীশচন্দ্র লিখলেন -
‘তুমি তো এতদিন নির্জ্জনে সাধনা করিয়াছ, বলিতে পার কী, কী করিলে সুখদুঃখের অতীত হইতে পারা যায়? একদিন ভারতে সুদিন আসবেই, কিন্তু একথা সর্বদা মনে থাকে না। ইহা যে সত্য একথা আমার মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়।’
১০ মে বিলেতে পরীক্ষা দিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। দু’দিন আগে ৮ মে তাঁর মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় নিচের চিঠিতে -
‘আমি যে কি কষ্টের ভেতর দিয়া যাইতেছি তুমি জানিবে না। তোমরা নিরাশ হইবে একথা মনে করিয়া আমি এখানে কিরূপ বাধা পাইতেছি তা জানাই নাই।... এই যে গত বৎসর মে মাসে যে আবিষ্কার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম……। আমার সেই আবিষ্কার চুরি করিয়া ... নভেম্বর মাসে এক কাগজে বাহির করিয়াছে!’
আসলে লিনিয়ান সোসাইটির কাউন্সিল সভায় যখন ঠিক হয় যে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাপত্রটি ছাপা হবে, তখন বিজ্ঞানী এর বন্ধু বিজ্ঞানীরা কাউন্সিল সভায় জানান যে, এমন কাজ নাকি একজন গত নভেম্বরে প্রকাশ করেছেন। এ কাজের আর কোন গুরুত্ব নেই। জগদীশচন্দ্রের গবেষণাপত্রটি তাই মুদ্রণের জন্য বিবেচিত হতে পারে না।
একসময় কথাটা জগদীশচন্দ্রের কানে যায়। জগদীশচন্দ্র সব জানিয়ে লিনিয়ান সোসাইটির সভাপতিকে চিঠি লেখেন। সভাপতি তাঁকে একসময় জানান, ভুল বুঝতে পেরেছেন ওঁরা।
তখনই জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন -
‘.... ভাঙিয়া গেলে আর কি থাকে। এতদিন এদেশের বিজ্ঞানসভায় অনেক বিশ্বাস করিয়াছি_ তাহা দূর করিয়া লাভ কি? অধিক দিন থাকিতে পারিলে আমি একাই বূহ্য ভেদ করিতাম_ কিন্তু আমার মন ভাঙিয়া গিয়াছে।’
১ মে জগদীশচন্দ্র লিখছেন, ‘একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়। ৮ মে লিখছেন, ‘... আমার মন ভাঙিয়া গিয়াছে।’
বিজ্ঞানীর এই মানসিক বিষণ্নতা অনুভব করে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে বারবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর প্রতিভা যে ব্যতিক্রমী, একথা কবি তাঁকে অনেকবার নানাভাবে বুঝিয়েছেন।
জগদীশচন্দ্র প্রতুত্তরে লিখছেন, ‘তুমি কি মনে কর যে আমি এক কেষ্টবিষ্টু হইয়াছি। গলায় পাথর বান্ধিয়া জলে ফেলিলে ভাসিয়া উঠিব?’ (৩০ মে, ১৯০২)।
রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে জগদীশচন্দ্রকে বারবার উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। আর স্বদেশে তাঁর কাজের বিষয়ে, তাঁর সাহসী লড়াইয়ের বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করা উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। সেই বিবেচনাবোধ থেকেই ‘আচার্য জগদীশের জয়বার্তা’ রচিত হয়েছে।
আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুখোমুখি পরিচয় হয় ১৯২৬ সালে। কবি তখন দ্বিতীয়বার জার্মানি গিয়েছেন। হিটলারের উত্থান তখনও স্পষ্ট হয়নি। কী আলোচনা হয়েছে দু’জনের সে সময়, কোন লেখাপত্র বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের মনে যে শ্রদ্ধার রেখা টেনেছিলেন, ১৯২৬ সালে লেখা আইনস্টাইনের একটি চিঠি থেকে সে প্রমাণ পাওয়া যায়। চিঠির তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬। ছোট্ট চিঠি, দু’একটি লাইন উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।
মাননীয় আচার্য,
... আপনাকে স্বচক্ষে দেখে আসতে না পারার জন্য দুঃখিত। শুনেছি আপনার উপর প্রচুর ধকল গেছে। তাই ভিড় বাড়িয়ে আপনার বিশ্রাম এবং শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি। জার্মানিতে যদি এমন কিছু থাকে যা আপনি চান এবং যা আমি করতে পারি, দয়া করে, যখন খুশি আমায় আদেশ করবেন।”
আইনস্টাইন ১৯২৬ সালে অপরিচিত কেউ নন। নোবেল জয় করেছেন পাঁচবছর আগে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর এমন নিবেদন আমাদের অন্য একটি ঘটনার কথাও মনে করিয়ে দেয়। ১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথের যে বিখ্যাত গবেষণাপত্র বেরিয়েছিল তাঁর জন্য আইনস্টাইনের ভূমিকা কী ছিল আমরা জানি। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন অপরিচিত যুবক। তিনি আইনস্টাইনকে গভীর বিনয়ী চিঠি লিখতেই পারেন। আইনস্টাইনের লেখা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে চিঠি আমাদের আইনস্টাইনের প্রতি শ্রদ্ধা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। রবীন্দ্র প্রতিভার বিশ্বজনীনতাকে বুঝতে সহায়তা করে।
আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের দিনটি ছিল ১৪ জুলাই, ১৯৩০। বিশ্বের বহু সংবাদপত্রে তার সবিস্তার বিবরণী বেরিয়েছিল। ‘প্রবাসী’ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত ‘গোল্ডেন বুক অব টেগোর’-এ সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই বইয়ে আইনস্টাইন নিজে রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি লেখাও দিয়েছিলেন। ১৪ জুলাই বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা বিষয় নিয়ে দু’জনের কথাবার্তা হয়েছে। এমনকি আলোচনায় ঈশ্বর প্রসঙ্গও এসেছে। আইনস্টাইন তখন বার্লিন থেকে খানিকটা দূরে কাপুথ নামে একটা ছোট্ট শহরে থাকতেন। আইনস্টাইনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ যান। দু’জনের বেশ খানিকটা সময় ধরেই কথা হয়। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তাঁর বইতে লিখেছেন-’কোথাও কি তাঁদের মিল ছিল না? অবশ্যই ছিল। দু’জনেই আদর্শবাদী ছিলেন। দু’জনেরই প্রবল বিশ্বাস ছিল ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার অধিকার। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সেই বিপন্ন সময়ে দু’জনেই বিশ্বশান্তির সপক্ষে কাজ করেছিলেন এবং সে-বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। আধুনিক রাষ্ট্রশক্তির প্রবল প্রতাপ সম্বন্ধে দুজনেই প্রতিকূল ছিলেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার দিক দিয়ে তাঁদের মনে মিল ছিল।’
১৪ জুলাইয়ের পর ১৯৩০ সালে আরও তিনবার দু’জনের দেখা হয়। ১৯ আগস্ট বার্লিনে দেখা হয়। সেপ্টেম্বরের শেষে আবার বার্লিনে দেখা হয়। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিউইয়র্কে দেখা হয়। দু’জন বড় মাপের মানুষ এক বছরে চারবার পরস্পর মিলিত হচ্ছেন, হৃদমাঝারে কোন আত্মীয়তা না থাকলে তা কখনও সম্ভব হয়ে উঠতে পারে না।
ওই সময় ১৯ আগস্ট কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। একটু বিষয় বদলে যায়। আইনস্টাইন প্রথম ক’বছর কোয়ান্টাম তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। সে কথার ইঙ্গিত আমরা আগে রেখেছি। কথায় কথায় সঙ্গীত প্রসঙ্গ চলে এল। পুবের সঙ্গীত ও পশ্চিমের সঙ্গীত নিয়ে কথা হলো। রবীন্দ্রনাথ বললেন, পাশ্চাত্যে স্বরলিপি কঠোরভাবে মানতে হয়। ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরলিপি থাকলেও শিল্পীদের স্বাধীনতা রয়েছে। ফলে সঙ্গীতকে ‘শিল্প’ করে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে। আইনস্টাইন জানতে চেয়েছিলেন, ভারতীয় সঙ্গীতে বাণীর প্রাধান্য কেমন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, উত্তর ভারতে কম, বাংলায় বেশি। কতটা বাদ্যযন্ত্র থাকে, জানতে চাইলেন আইনস্টাইন। রবীন্দ্রনাথের উত্তর ছিল, পশ্চিমি গানের ‘হারমনি’ তৈরির জন্য নয়। তাল ও মাত্রা ঠিক রাখার জন্য বাদ্যানুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অন্যতম মেধাবী ছাত্র ছিলেন প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা ‘বিশ্বপরিচয়’ এর সাথে তাঁর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ একবার প্রমথনাথকে বলেছিলেন - ‘শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেও না, এখানে তোমার প্রয়োজন আছে... যেদিন দেখবে এখানে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, শিক্ষার চেয়ে শাসনযন্ত্রটাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, সেদিন তুমি চলে যেও।’
সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছেন, ‘এই পুণ্যকাজে আমার আশীবার্দ রইল।’ (আনন্দরূপম পৃষ্ঠা ১৬৩-৬৪)
এখানে আমাদের আলোচনার বিশেষ সুযোগ নেই। তবু মনে রাখতে হয়, শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানকে তাঁর ভাবনার অন্যতম প্রধান উপজীব্য বিষয় করে তুলেছিলেন। আগেই বলেছি, ছিয়াত্তর বছর বয়সে ‘বিশ্বপরিচয়’-এর পাণ্ডলিপি প্রস্তুত করেছেন তিনি। জীবন সায়াহ্নে তাঁর ‘তিন সঙ্গী’ গল্পগ্রন্থ, যা ‘রবিবার’, ‘শেষ কথা’ ও ‘ল্যাবরেটরি’ নামের তিন বিখ্যাত ছোট গল্পের সংকলন, সেখানেও তিনি বিজ্ঞান চিন্তাকেই গল্প তিনটির মূল ভাবনা হিসাবে পেশ করেছেন। তিন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রেরা সকলে জীবিকাসূত্রে ‘বিজ্ঞান’ নির্বাচন করেছিলেন। গল্পের শেষে দেখা যায়, তারা সকলেই অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের জালে বাঁধা পড়ে আছেন। ‘সমগ্র’ বিজ্ঞানকে অনুভব করার কথা বলতেন তিনি। ‘বিশ্বপরিচয়’ গ্রন্থে তথ্যের প্রাচুর্য থাকলেও এই ভাবনাকেই তিনি চূড়ান্ত রূপ দিতে চেয়েছেন। আমরা বলব, সার্থক হয়েছে তাঁর এই চাওয়া।
তাঁর বিজ্ঞানশিক্ষা বা বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস যাই হোক, এটা সত্যি এক অভাবিত বিজ্ঞানবোধ তাঁর মনন ও কল্পনা উভয়কেই আচ্ছন্ন করেছিল। তার একটি উপাদান হলো এই বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। খুব অল্পবয়সেই এই অস্তিত্বের বিশাল পরিসর সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বুঝে উদ্ভাসিত হয়ে ‘আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ’ সম্বন্ধে তার একটি বোধ তৈরি হয়েছিল। এই বোধ তার কবিত্বকে সমৃদ্ধ করেছে, কারণ এর উৎস বিজ্ঞান হলেও এর মধ্যে জন্ম দিয়েছে এমন এক বিস্ময়, তাই বলেছিলেন -
‘তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ..
(বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে সংকলন করে লেখা)
(আমার কণ্ঠস্বর বা বাচনভঙ্গি কোনোটাই ভালো নয়। তবুও এই প্রথম লেখা পাঠ করলাম। ভুলত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করবেন।)
https://youtu.be/5UlYa2N2As4