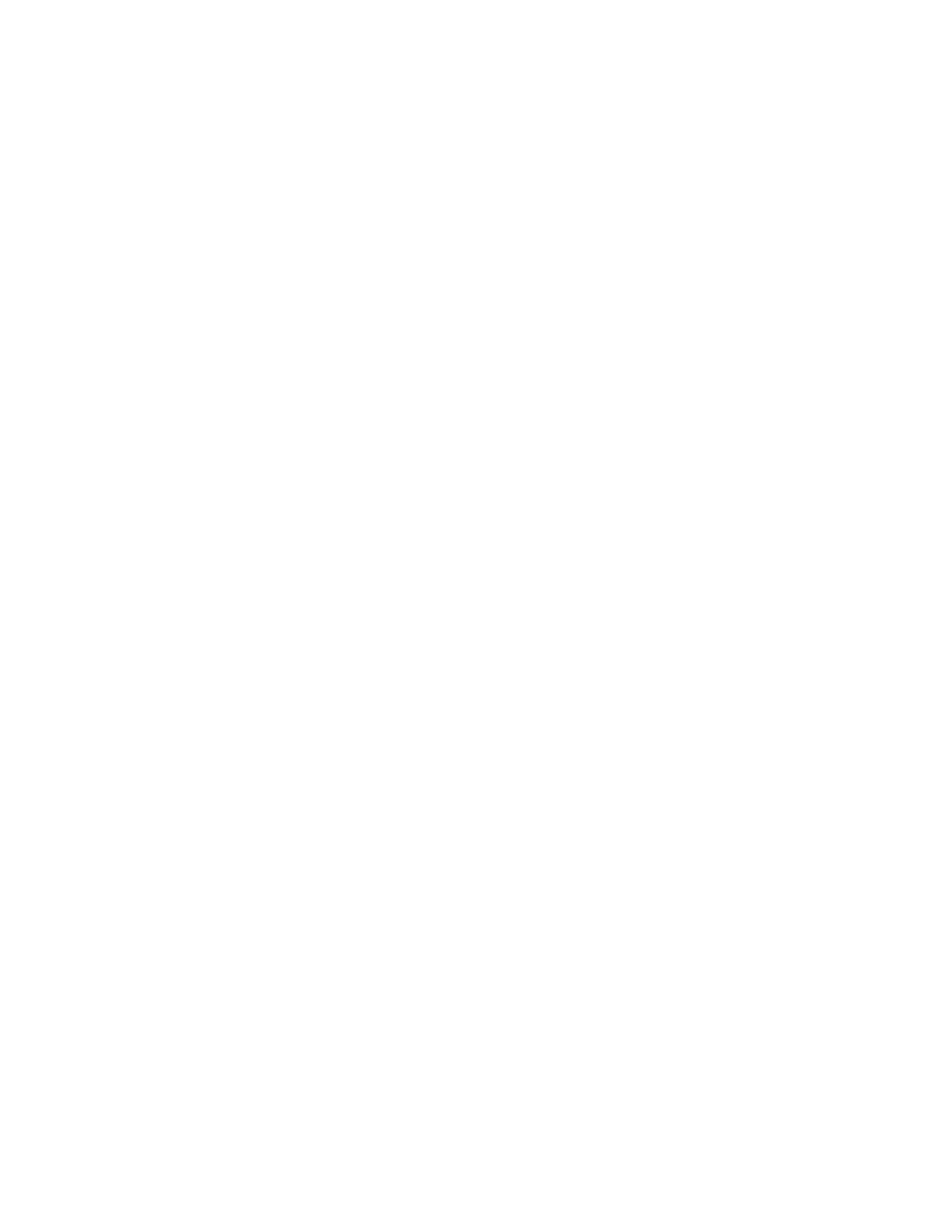ডিরোজিও: যে ঝড়ের পাখিকে প্রয়োজন আজও
অভিষেক দে
May 19, 2025 | | views :6 | like:0 | share: 0 | comments :0
শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর “রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” গ্রন্থে লিখেছেন- “চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি তিনিও তাঁর বালকদিগকে আকর্ষণ করিতেন”। সেই চুম্বকটির আজ জন্মদিন। উনি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ওনার জন্ম ১৮ এপ্রিল, ১৮০৯।
ডিরোজিও একজন ইউরেশীয় কবি, মুক্তমনা চিন্তাবিদ এবং শিক্ষক। তবে দুঃখের বিষয় খুবই অল্পবয়সেই এই তরুণ প্রাণ অকালে শেষ হয়ে যায় কলেরা রোগে (২৬ ডিসেম্বর, ১৮৩১)। অনেকেই হয়ত জানেন না, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিশিষ্ট অভিনেতা উৎপল দত্তের পরিচালনায় ১৯৮২ সালে ডিরোজিয়োর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাঁর জীবনের শেষ দুই বছরকে ভিত্তি করে “ঝড়” নামক একটি সিনেমা তৈরি হয়। “ঝড়” সিনেমাটির মোট ১২ টি পার্ট আছে।
ডিরোজিও কলকাতার এন্টালি-পদ্মপুকুর অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও ছিলেন একজন খ্রিস্টান ইন্দো-পর্তুগিজ অফিস কর্মী এবং তাঁর মাতা ছিলেন সোফিয়া জনসন ডিরোজিও।
ডিরোজিও, ডেভিড ড্রুমন্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমি স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছিলেন, যেখানে তিনি ছয় থেকে চোদ্দো বছর পর্যন্ত একজন ছাত্র ছিলেন এবং ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ১৭ বছর বয়সে ডিরোজিও নতুন হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্য এবং ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন।
তখনকার সময়ে ইয়ং বেঙ্গলের তরুণেরা ছিলেন বেশ চঞ্চল প্রকৃতির। তাঁদেরকে সন্ধ্যা বেলায় জোর করে ঠাকুর ঘরে নিয়ে গেলে সেখানে বসে ধর্মগ্রন্থ পড়বার পরিবর্তে হোমার, ইলিয়ডের বই থেকে উদ্ধৃতি পাঠ করতেন। দেবদেবীকে প্রণাম করার পরিবর্তে বলতেন, ‘গুড মর্নিং, ম্যাডাম/স্যার। দিনের বেলা লোকজনকে দেখিয়ে গোমাংস ও মুসলিমদের হাতেগড়া রুটি খেয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের খাদ্যবিধিতে আঘাত করতেন। হিন্দুদেবী কালীকে নিয়ে ছড়া কাটতেন, হাতের নাগালে কোনও ব্রাহ্মণ পেলে “আমরা গরু খাই গো” বলে উত্যক্তও করতেন। এভাবে হিন্দুদের জাত্যাভিমানে বা বলা ভালো তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানার জন্য যত ধরনের দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় আসতো, তার সবটুকুর প্রয়োগ তাঁরা করতেন।
ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ডিরোজিও তাঁর অনুগামীদের অর্থাৎ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে যে সংগঠন গড়ে তোলেন সেটি, “ইয়ংবেঙ্গল বা নব্যবঙ্গ” নামে পরিচিত। এই সংগঠনের উদ্দ্যেশ্যে ছিল- (১) তরুণপ্রজন্মের মধ্যে যুক্তিবোধ, বিজ্ঞানমনষ্কতার বিকাশ ঘটানো। (২) নারীদের উচ্চশিক্ষিত গড়ে তোলা, (৩) সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং জাতপাত ইত্যাদির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা এবং এইসকল বিষয়ে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসু মনন গড়ে তোলা, (৪) স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটানো (৫) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ইত্যাদি। এইপ্রসঙ্গে জানাই, ১৮২৮ সালে কলকাতার মানিকতলা এলাকায় “অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন” প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সমাজের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে কাজকর্মের জন্যেই।
ডিরোজিও তার মাত্র ২২ বছরের জীবনে এমন বেশকয়েকটি কাজ করে গেছেন যা সত্যি অবাক করার মতন। জীবনে চূড়ান্ত আর্থিক এবং সামাজিক অবরোধের মধ্যে পড়েও তিনি যতদূর এগোতে পেরেছিলেন তা অকল্পনীয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে ডিরোজিও কি সত্যিই যুক্তিবাদী ছিলেন বা ওনাকে কে কি যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনষ্ক বলা যাবে?
এইপ্রশ্নের উত্তরে কিছু খোলামেলা আলোচনা করা যেতে পারে, যেমন- পৃথিবীতে এমন কেউই নেই যে বা যিনি সম্পূর্ণ দোষত্রুটি মুক্ত। তাই সমালোচনার ঊর্ধেও কেউ নন। কোন মানুষকে সঠিক বিচার করতে গেলে দেশ, কাল, সামান্যই পরিস্থিতি এরূপ বিবিধ বিষয় বিবেচনা করতে হয়।
ডিরোজিও যেসময় জন্মেছিলেন তখন পরাধীন ভারতে সেই সময় কারো পক্ষে কতটুকুই বা বিজ্ঞানমনস্ক বা আরও ভালোভাবে বললে সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী হওয়া সম্ভব ছিল?তবে ডিরোজিও নিজ সময়ের থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে ছিলেন। আক্ষরিক অর্থেই তিনি তার পারিপার্শ্বিক সমাজে চিন্তা, চেতনার, বিজ্ঞানমনস্কতার এমন এক প্রচন্ড ঝড় তুলেছিলেন যাকে সামাল দিতে বেসামাল হয়েছিল তৎকালীন উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজ। এইজন্যই কি তিনি শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারেন না? ডিরোজিও ছিলেন খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান
গির্জা ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে তাঁর অভিমতের কারণে তাঁর মৃত্যুর পরে পার্কস্ট্রিটের গোরস্থানে তাকে সমাহিত করতে বাধা দেওয়া হলে গোরস্থানের ঠিক বাইরে তাকে সমাহিত করা হয়।
ইয়ংবেঙ্গল বা নব্যবঙ্গীয় গোষ্ঠীর সদস্যগণ ছিলেন রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখােপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র,লালবিহারী দে, মাধবচন্দ্র মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র দেব, কিশোরী চাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাধানাথ শিকদার, কাশীপ্রসাদ প্রমুখরা। ডিরোজিওর অকাল মৃত্যুর পরে বহু ডিরোজিয়ান অধঃপতিত হয়ে আবার হিন্দুয়ানী, বাবু কালচারের চোরাস্রোতে ডুবে গিয়েছিল যদিও তার দায় অবশ্য ডিরোজিওর হতে পারেনা।
এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৮৮২ সালে গড়ে ওঠে “Bengal Theosophical Society” যার সভাপতি হয়েছিলেন একদা ডিরোজিয়ান পন্থী, বুদ্ধিজীবী, যুক্তিবাদী হিসেবে চিহ্নিত প্যারীচাঁদ মিত্র। সংগঠনটির সহ-সভাপতি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর ও শ্যামাশংকর রায় সহ অনেকেই যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন আইরিশ রমনী, থিওসফিস্ট আনি বেশান্ত যিনি ১৮৯৩ সালে ভারতে আসেন এবং সাড়াজাগিয়ে প্রেতচর্চা শুরু করেন।
ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যরা যে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিল তা ডিরোজিওর মৃত্যুর পরও সক্রিয় ছিল। কিন্তু ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সাফল্য ছিল খুবই সামান্য। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন পণ্ডিত ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করে জানিয়েছেন-
(১) নেতিবাচক ভাবাদর্শ: ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সমস্ত কর্মসূচিই ছিল নেতিবাচক। তাঁদের কোনো গঠনমূলক কর্মসূচি ছিল না। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সবকিছু না জেনেই তারা এই ধর্মের বিরোধিতায় উগ্রভাবে সোচ্চার হন। অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কেও তাঁদের কোনোও স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। তাদের এই কালাপাহাড়ি মনোভাবের জন্য হিন্দুসমাজ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।
(২) জনসমর্থনের অভাব: ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের আন্দোলনকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারেননি। ড. সুমিত সরকার বলেছেন যে, মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী অংশ ছাড়া বাঙালি সমাজের বৃহত্তর অংশের ওপর ইয়ং বেঙ্গল মতাদর্শের কোনোও প্রভাব পড়েনি।” অভিজাত পরিবারের শহরের কিছু তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল।
(৩) সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অনেকেই ইংরেজ কোম্পানির সহযোগী হিসেবে বিলাসবহুল জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেন। সমাজের সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষক শ্রমিকের সঙ্গে তাঁদের কোনোও যোগাযোগ ছিল না।
(৪) উগ্রতা: ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যদের উগ্র ও অতি বিপ্লবী কার্যকলাপ সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। তাই কলকাতার এলিটিস্ট সমাজে এবং পত্রপত্রিকার মধ্যেই তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক ডেভিড কফ তাঁদের ভ্রান্ত পুঁথি-পড়া বুদ্ধিজীবী বলে অভিহিত করেছেন।
(৫) দরিদ্রদের প্রতি উদাসীনতা: ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী দেশের দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের দুরবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট কৃষকদের দুর্দশা এবং কুটিরশিল্প ধ্বংসের ফলে দরিদ্র সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্দশা থেকে মুক্ত করার কোনোও উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেননি।
(৬) মুসলিম-বিচ্ছিন্নতা: ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন শুধু হিন্দু সমাজের সংস্কার নিয়ে চিন্তাভাবনায় ব্যস্ত ছিল। মুসলিম সমাজের সংস্কার নিয়ে গোষ্ঠীর সদস্যরা কোনোও চিন্তাভাবনা করেননি।
(৭) সংস্কারবিমুখতা: ডিরোজিওর মৃত্যুর পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীদের অনেকেই সংস্কারবিমুখ হয়ে সংস্কার কর্মসূচি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। অনেকে সরকারি চাকরি বা ব্যাবসায় মনোযোগ দিয়ে নিজেদের সংসার জীবনে উন্নতির চেষ্টা করেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রমুখ ডেপুটি কালেক্টর এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন।
পরিশেষে জানাতে চাই, এই ক্ষণজন্মা মানুষটির আজ বড়ই প্রয়োজন। যে ঝড়ের বেগে আসবেন এবং ভেঙ্গেচুরে একাকার করে দিয়ে যাবে সমস্ত অন্ধভক্তি, উগ্রদ্বেষপ্রেম, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, জাতপাত, বিদ্বেষের রাজনীতি। আজ বিশ্বজোড়া অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটা সংঘর্ষ খুবই জরুরি। তারপরেই হবে নির্মাণ, একটা সুস্থ, সুন্দর সমাজের।